ডাকঘর নাটকের প্রশ্ন উত্তর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) | ক্লাস 12 বাংলা চতুর্থ সেমিস্টার | Daakghor natoker long question answer
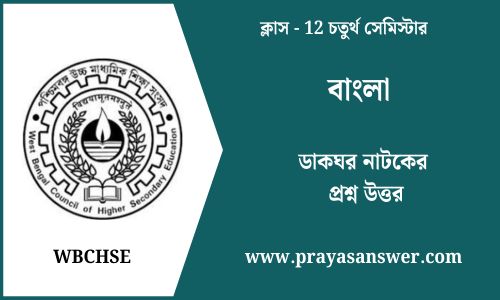
১। “ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।”-কে, কার সম্পর্কে কোন্ প্রসঙ্গে মন্তব্যটি করা হয়েছে? এর কোন্ প্রতিক্রিয়া উল্লিখিত চরিত্রের মধ্যে ঘটেছিল? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে কবিরাজ মাধব দত্তকে উদ্দেশ করে অমল সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
অমল অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার পালক পিতা মাধব দত্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কবিরাজমশায়ের পরামর্শ চান। কবিরাজমশায় সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করে বলেন যে, অমলকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। মাধব দত্ত এই সাবধানে রাখার বিষয়টি স্পষ্ট করতে বললে কবিরাজ বলেন যে, তিনি আগেই বলে দিয়েছেন-অমলকে একেবারেই বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না।
মাধব দত্ত কবিরাজের পরামর্শ কার্যকর করা নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন। ছেলেমানুষ অমলকে দিনরাত ঘরের মধ্যে আটকে রাখা যে খুবই শক্ত তা তিনি স্পষ্টভাবেই জানান। কবিরাজ বোঝাতে চান যে, শরৎকালের রৌদ্র এবং বাতাস উভয়ই অমলের জন্য খারাপ। মাধব দত্ত অমলকে ঘরে বন্ধ করে রাখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে কি না জানতে চান। কিন্তু কবিরাজের কাছ থেকে কোনো সদর্থক উত্তর না পেয়ে বলেন যে, তাঁর নির্ধারিত ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। অমল তার অসুখের সমস্ত কষ্ট চুপ করে সহ্য করতে পারে কিন্তু কবিরাজের ওষুধ খাওয়ার সময় তার কষ্ট দেখে মাধব দত্তের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।
২। “…উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।” -বক্তার পরিচয় দাও। তাঁর এই আনন্দের কারণ আলোচনা করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকের উল্লিখিত মন্তব্যটির বক্তা মাধব দত্ত।
মাধব দত্তের নিজের কোনো সন্তান ছিল না। অমল ছিল পিতামাতৃহীন এক অনাথ কিশোর। তাঁর স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কের ভাইপো। মূলত স্ত্রীর ইচ্ছায় মাধব দত্ত অমলকে দত্তক নেন। একসময় তাঁর এই দত্তক নেওয়ার বিষয়টি পছন্দ ছিল না। বহু পরিশ্রমে যে বিপুল টাকা তিনি সঞ্চয় করেছেন, তা অন্যের সন্তান এসে বিনা পরিশ্রমে নষ্ট করবে তা তিনি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু অমলকে পোষ্যপুত্র হিসেবে পেয়ে তাঁর ভাবনা পালটে যায়। এই প্রসঙ্গেই মাধব দত্ত বলেছেন যে, আগে তাঁর কাছে রোজগার ছিল নেশার মতো। তা না করে তিনি থাকতে পারতেন না। কিন্তু বর্তমানে যে টাকা উপার্জন করছেন তার সবটাই তাঁর দত্তক ছেলে পাবে জেনে মাধব দত্তের উপার্জনের আনন্দ বেড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রতি তীব্র আসক্তি ও মোহগ্রস্ততার সঙ্গে অমলকে কেন্দ্র করে মাধব দত্তের মধ্যে যুক্ত হয়েছিল বাৎসল্যের স্নেহকাতরতা।
৩। “তাই তোমাকে ভয় করি।” -কে, কাকে উদ্দেশ করে এ কথা বলেছেন? এ কথা বলার কারণ কী? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে উদ্দেশ্য করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
মাধব দত্তের বাড়িতে ঠাকুরদার আগমন ঘটলে মাধব দত্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কারণ তাঁর মতে ঠাকুরদা ছিলেন ‘ছেলে খেপাবার সদ্দার’। মাধব দত্তের চিন্তার কারণ তিনি অমলকে ‘পোষ্যপুত্র’ নিয়েছেন। তার প্রতিই যে তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত তা মাধব দত্ত স্পষ্টভাবে জানান। তিনি বলেন যে, আগে টাকা রোজগার করা তাঁর কাছে নেশার মতো ছিল, কিন্তু এখন সব উপার্জন তাঁর পোষ্য ছেলের জন্য ভেবে তাঁর মনে ‘ভারি একটা আনন্দ’ হয়। ঠাকুরদার প্রশ্নের উত্তরে মাধব দত্ত জানান যে, ছেলেটি তাঁর স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কের ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে তার মা নেই, আবার কয়েকদিন আগে তার বাবাও মারা গিয়েছে। একথা শুনে ঠাকুরদা বলেন যে, সেই কিশোরের তাঁকে দরকার আছে। মাধব দত্ত এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই বলেন যে, অমলের শরীরে একসঙ্গে যেভাবে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রকূপিত হয়েছে তাতে কবিরাজ বলেছেন যে, তার বাঁচার খুব একটা আশা নেই। শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলে তাকে বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু ঠাকুরদা সেক্ষেত্রে চিন্তার কারণ। যেহেতু ‘ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই’ তাঁর ‘বুড়োবয়সের খেলা’, সে কারণেই মাধব দত্ত তাঁকে ভয় করতেন।
৪। “বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো…।”-কাকে উদ্দেশ করে, কে মন্তব্যটি করেছেন? মন্তব্যটির তাৎপর্য লেখো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে মাধব দত্ত অমলকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
কবিরাজ অসুস্থ অমলকে সুস্থ করে তোলার জন্য ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে বলেছিলেন, যাতে শরতের রোদ আর বাতাস তাকে ছুঁতে না পারে। কিন্তু অমলের মনে বাইরে যাওয়ার জন্য স্বাভাবিক আকুলতা। উঠোনের যেখানটায় পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন, আর কাঠবিড়ালি সেই ভাঙা ডালের খুদ দু-হাতে তুলে নিয়ে ল্যাজের উপরে ভর করে খেতে থাকে, সেখানে অমল যেতে চায়। কিন্তু পিসেমশাই মাধব দত্ত কবিরাজের নিষেধের কথা বলেন। কবিরাজ যেহেতু বড়ো বড়ো পুথি পড়ে ফেলেছেন তাই তাঁর জানা অভ্রান্ত বলে মাধব দত্ত মনে করেন। পুথি পড়লে সব জানা যায় শুনে অমল আক্ষেপ করে, কারণ তার কোনো পুথিই পড়া হয়নি। এই সময়েই তারা ঘর মাধব দত্ত বলেন যে, পন্ডিতেরা সকলে অমলের মতো, থেকে বেরোয় না। এ কথার মধ্য দিয়ে মাধব দত্ত বলতে চেয়েছেন যে, সমস্তক্ষণ পুথি পড়ার পরে তাঁরা অন্য কোনো দিকে তাকানোর অবসর পান না। অর্থাৎ পণ্ডিতরা যে বাস্তববিমুখ এবং পুথিসর্বস্ব-তা নিয়েই তির্যক ইঙ্গিত উঠে আসে মাধব দত্তের কথায়।
৫. “…. তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না” -কে, কাকে উদ্দেশ করে মন্তব্যটি করেছে? তার পণ্ডিত হতে না চাওয়ার কারণ কী?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল মাধব দত্তকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছে।
কবিরাজের নির্দেশমতো অসুস্থ অমলকে সুস্থ করার জন্য ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু অমলের মন বাইরে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। উঠোনের যেখানটায় পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন, আর কাঠবিড়ালি সেই ভাঙা ডালের খুদ দু-হাতে তুলে নিয়ে ল্যাজের উপরে ভর করে খেতে থাকে- সেখানে অমল যেতে চায়। মাধব দত্ত কবিরাজের নিষেধের কথা বলেন। শুধু তাই নয়, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা তার মতোই ঘর থেকে বেরোয় না, ঘরে বসে তারা শুধু পুথি পড়েন-এ কথাও তিনি বলেন। আর এভাবে অমলও বড়ো হলে একদিন পণ্ডিত হয়ে উঠবে, “বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে”- সে কথাও তিনি জানান। তখনই অমল পণ্ডিত হতে তার তীব্র আপত্তির কথা জানায়। কারণ পণ্ডিতদের পুথি ছাড়া অন্য কোনো দিকে চোখ নেই, আর অমলের এই পৃথিবীর সবকিছু দেখে বেড়ানোতেই আনন্দ। জানলার কাছে বসে যে পাহাড় দেখা যায়, অমলের ইচ্ছে সেই পাহাড় পার হয়ে চলে যাওয়ার। পৃথিবী কথা বলতে পারে না, তাই যেন নীল আকাশে হাত তুলে তাকে ডাকে। পুথির মধ্যে নয়, মুক্ত দিগন্তে অবাধ বিচরণে অমল তার আত্মার আনন্দ খুঁজে পায়। তাই সে পণ্ডিত হতে চায়নি।
৬। “কিন্তু আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায়না-সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।” বক্তার এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে অমলকে সুস্থ করার জন্য কবিরাজের নির্দেশমতো ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু অমলকে হাতছানি দিত বাইরের পৃথিবী। নীল আকাশে হাত তুলে পৃথিবী যেন তাকে ডাক পাঠায়। জানলার সামনে বসে থাকা অমলের মন টেনে নেয় একটা ‘খেপা’ লোক। তার কাঁধে একটা বাঁশের লাঠি, বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরোনো একজোড়া নাগরাজুতো পরে সে এই মাঠের পথ ধরে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল ‘কাজ খুঁজতে’ নিরুদ্দেশ গন্তব্যে। ডুমুরগাছের তলা দিয়ে যেখানে ঝরনা বয়ে যাচ্ছিল, সেখানে সে পা ধুয়ে, ছাতু জল দিয়ে মেখে খেয়েছিল। অমলও সেখানেই যেতে চেয়েছিল। মাধব দত্ত অমলকে বলেছিল যে, ভালো হলে সে সেখানে যাবে এবং সেই সঙ্গে বিদেশি লোককে ডেকে কথা বলতে সে অমলকে নিষেধ করে। কিন্তু অমল স্পষ্ট জানায় যে, বিদেশি লোক তার ভালো লাগে। তাকে ধরে নিয়ে গেলে ভালো হত, কিন্তু কেউ তাকে ধরে নিয়ে যায় না, ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দেয়। মুক্ত জীবনের আকর্ষণ আর তার কাছে পৌঁছাতে না পারার হতাশা অমলের কথায় উঠে আসে।
৭। “দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।” -কে, কাকে উদ্দেশ করে মন্তব্যটি করেছেন? তার এই মন্তব্যের কারণ কী? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে দইওয়ালা অমলকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে দইওয়ালা অমলকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
জানলার সামনে বসে থাকা অমলের মন উন্মনা হয়ে ওঠে দইওয়ালার ডাকে। সে দইওয়ালার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চায়। তার মনে হয় পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী নদীর ধারে দইওয়ালার গ্রাম সে দেখেছে। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে। মেয়েরা সব লাল শাড়ি পরে নদী থেকে জল নিয়ে আসে। দইওয়ালা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে যে, বাস্তবের সঙ্গে অমলের ধারণা অধিকাংশই মিলে যায়। কবিরাজ তাকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিলে সে দইওয়ালার গ্রামে যাবে বলে জানায়। দইওয়ালার কাছে সে আগাম আবেদন জানিয়ে রাখে তাকে বাঁক কাঁধে নিয়ে দূরের রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার এবং দই বিক্রি শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। দইওয়ালার কাছে সে শিখে নিতে চায় দই বিক্রির সুর। রাস্তার মোড় থেকে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে দইওয়ালার ডাক যখন সে শুনতে পায় তার মন উদাস হয়ে যায়। অমলের এইসব কথা দইওয়ালাকে মুগ্ধ করে। তাই অমল যখন সংশয় প্রকাশ করে, সে দইওয়ালার দেরি করে দিল কি না তখন দইওয়ালা উচ্ছ্বসিতভাবে উল্লিখিত মন্তব্যটি করে।
৮। “আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই-” -বক্তাকে অনুসরণ করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল প্রহরীকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছে।
প্রহরীকে রাস্তায় পায়চারি করতে দেখে অমল তাকে ডাকতে থাকে। তাকে অমলের ভয় করে না। বরং প্রহরী তাকে ধরে নিয়ে যাবে বললে, সে জানতে চায় তাকে অনেক দূরে পাহাড় পেরিয়ে কোনো জায়গায় ধরে নিয়ে যাওয়া হবে কি না। অর্থাৎ সেই ধরাকেও সে মুক্তির উপায় বলেই দেখতে চেয়েছে। এমনকি কবিরাজের নিষেধ না থাকলে প্রহরীর কথামতো রাজার কাছে যেতেও তার আপত্তি ছিল না। প্রহরীর ঘণ্টার শব্দও অমলের ভালো লাগে। যখন দুপুরবেলা বাড়ির সকলের খাওয়া হয়ে যায়, পিসেমশাই কোথাও কাজে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, এমনকি বাড়ির খুদে কুকুরটাও উঠোনে কোণের ছায়ায় ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে তখন প্রহরীর ঘণ্টা বেজে ওঠে। প্রহরী বলে যে, তার ঘণ্টা সবাইকে জানিয়ে দেয় “সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।” কোন্ দেশে সেই সময় চলে যাচ্ছে তা কেউ জানে না। প্রহরীর এ কথা শুনেই অমল বলে যে, তার খুব ইচ্ছে করে সেই সময়ের সঙ্গে চলে যেতে, যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরের দেশে। গৃহবন্দী অমলের বাইরের জগতের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা নানা কিছুকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। প্রহরীর ঘণ্টার ধ্বনি সেরকমই একটা অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে।
৯। “বড়ো হলে আমি রাজার ডাক-হরকরা হব।” কখন এবং কেন বক্তা এই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছে। প্রহরী জানিয়েছিল যে, রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে। সেখানে রাজার কাছ থেকে চিঠি আসে। একদিন অমলের নামেও সেখানে চিঠি আসবে। অমল যখন শোনে যে, রাজার কাছ থেকে ডাক-হরকরা তার চিঠি এনে দেবে, আর কাজের সূত্রে তারা ঘরে ঘরে দেশে দেশে ঘোরে, তখনই অমল বড়ো হয়ে ডাকহরকরা হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে।
অমল চায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ। বদ্ধতা থেকে মুক্তি। তাই সে পণ্ডিত হতে চায় না। লাঠির ডগায় পুঁটলি বেঁধে যে লোকটা কাজ খুঁজতে বেরোয়, যে দইওয়ালা ‘দই দই ভালো দই!’ ডাক দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে যায়, অমল তাদের মতো বেরিয়ে পড়তে চায়। প্রহরীর ঘণ্টার ধ্বনি শুনে তার ইচ্ছা হয় সময়ের সঙ্গে চলে যেতে। রাজার ডাকহরকরার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছিল এই অনায়াস বাধাহীন বিচরণ। বুকে গোল গোল সোনার তকমা পরে যারা রোদ-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে, গরিব-বড়োলোকের ভেদ না করে সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ায় তাদের কাজকেই অমলের ‘সকলের চেয়ে ভালো’ বলে মনে হয়েছে। সেকারণেই সে বড়ো হয়ে ‘রাজার ডাকহরকরা’ হতে চেয়েছে।
১০। “শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি।” বক্তা কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলেছেন? এখানে তাঁর কোন্ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল মোড়লের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, রাজার ডাকহরকরা তার কথা শোনে কিনা। মোড়ল সম্মতিসূচক উত্তর দিলে অমল বলে, যদি তার নামে চিঠি আসে মোড়ল যেন ডাকহরকরাকে বলে দেয় যে, সে জানলার কাছে বসে থাকে। সে চিঠি তাকে কে লিখবে একথার প্রত্যুত্তরে অমল ‘রাজা’-র কথা বললে মোড়ল তাকে বিদ্রুপ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করে।
মোড়লের পক্ষে অমলের মনকে বোঝা সম্ভব ছিল না। প্রহরী এই মোড়ল সম্পর্কে জানিয়েছিল যে, সে ‘আপনি মোড়লি’ করে। “কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যবসা চালায়।” এরকম একজন লোকের পক্ষে অমলের সুদূর-বিহারী মনের সন্ধান পাওয়া ছিল অসম্ভব। তাই অমলের কথা মোড়লের বিদ্রুপের লক্ষ্য হয়। – “কদিন তোমার সঙ্গে দেখা না করে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে…… শুধু তাই নয়, রাজার চিঠির অপেক্ষায় থাকা অমলকে যে আশ্রয় দিয়েছে সেই মাধব দত্তও মোড়লের আক্রমণের লক্ষ্য হয়।- “দু-পয়সা জমিয়েছে কি না, এখন তার ঘরে রাজা-বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই।” অর্থাৎ একদিকে কিশোর অমলের মনকে বোঝার অক্ষমতা, অন্যদিকে প্রবল দম্ভ কার্যকরী থাকে মোড়লের আচরণে।
১১। “এখানে আমার আর-সব বন্ধ কেবল এইটুকু খোলা।” -বক্তা কাকে, কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে? তাকে উদ্দেশ করে বক্তা নিজের কোন্ ইচ্ছার কথা জানিয়েছে? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল সুধাকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছে।
মলের আওয়াজ তুলে সুধা যাচ্ছিল অমলের জানলার সামনে দিয়ে। অমল তাকে দাঁড়াতে বললেও সুধার দাঁড়ানোর সময় ছিল না। সেকথা শুনে অমল বলে যে, তারও বসে থাকতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কবিরাজ তাকে বেরোতে বারণ করেছে। সুধা অমলকে কবিরাজের কথা মেনে চলতে বলে, দুরন্তপনা না করতে বলে এবং যেহেতু বাইরের দিকে তাকিয়ে অমলের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে তাই সুধা অমলের অর্ধেক খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিতে চায়। এই প্রসঙ্গেই অমল তাকে জানলা বন্ধ করতে নিষেধ করে এবং উল্লিখিত মন্তব্যটি করে।
অমল যখন সুধার নাম জানতে পারে এবং আরও জানে যে, সে সেখানকার মালিনীর মেয়ে, সাজি ভরে ফুল তুলে এনে মালা গাঁথে, তখন সেও সুধার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। গাছের উঁচু ডাল যেখানে ফুল দেখা যায় না, সেখান থেকে সুধাকে ফুল পেড়ে দিতে চায়। সুধাকে অমল বলে যে, সে সাত ভাই চম্পার খবর রাখে। তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে চলে যেতে পারে খুব ঘন বনের মধ্যে, যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে দোল খায় সেখানে সে চাঁপা হয়ে ফুটতে পারে। অমল সুধার সঙ্গে গল্প করতে চায়। কারণ সুধা তার কাছে দূরদেশের আহ্বান। সুধা প্রতিশ্রুতি দেয় যে ফুল তুলে ফেরার পথে সে অমলের সঙ্গে গল্প করে যাবে। অমল তার কাছে একটা ফুল চায় এবং বলে যে, যখন সে বড়ো হবে তখন কাজ খুঁজে নিয়ে সুধার ফুলের দাম দিয়ে দেবে।
১২। “তোমরা আমার এই জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করো…” -কাদের উদ্দেশে বক্তা কখন এই মন্তব্য করেছে? তাদের খেলার জন্য বক্তা কীভাবে সাহায্য করেছিল? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল ছেলের দলকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছে।
অমল তার ঘরবন্দী জীবনে একমাত্র খোলা জানলার সামনে বসে ছেলের দলকে দেখেছিল, যারা খেলতে চলেছিল। অমলকে তারা বলেছিল যে তারা চাষ-খেলা খেলতে চলেছে। লাঠি তাদের লাঙল, দুজন বালক হবে দুই গোরু। তারা সমস্ত দিন খেলবে এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে আসবে। অমল তাদেরকে তার ঘরের সামনে দিয়েই ফিরতে বলে। ছেলের দল যখন এরপরে চলে যেতে উদ্যত হয়, সেই সময় অমল তাদের অনুনয় করে জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করার জন্য।
ছেলেরা যখন জানতে চায় যে তারা কী নিয়ে খেলবে, তখন অমল তার পড়ে থাকা সমস্ত খেলনা, যেগুলো তার একলা খেলতে ভালো লাগে না, তাদের দিয়ে দিতে চায়। ছেলের দল সেইসব খেলনা জাহাজ, জটাইবুড়ি, সেপাই ইত্যাদি অমল তাদের দিয়ে দিচ্ছে দেখে বিস্মিত হয়। অমল শুধু একটা শর্ত দেয়, তা হল-রোজ সকালে সেই খেলনাগুলো নিয়ে ছেলের দলকে তার দরজার সামনে কিছুক্ষণ খেলতে হবে। ছেলেরাও তাতে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু অমলের ঘুম আসায় এবং পিঠে ব্যথা হওয়ায় সেদিনের মতো তাদের খেলায় ছেদ পড়ে।
১৩। “তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাক-হরকরাদের চেন?” -বক্তার এই প্রশ্নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে ছেলের দলকে অমল তার খেলনাগুলো দিয়ে দেয় এবং সেই খেলনাগুলো নিয়ে অমল ছেলেদের প্রতিদিন সকালে তার বাড়ির সামনে খেলতে বলে। কিন্তু খেলার উদ্যোগ নিয়েও ছেলেরা অমলকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে সেদিনের মতো চলে যেতে উদ্যত হয়। তখন অমল তাদের কাছে জানতে চায় যে, তারা রাজার ডাকঘরের ডাকহরকরাদের চেনে কিনা। ছেলেরা বলে তারা চেনে, যেমন একজনের নাম বাদল হরকরা, একজন শরৎ হরকরা, এরকম আরও অনেকে আছে। অমল অপেক্ষা করে আছে যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে পাঠানো রাজার চিঠি এনে দেবে। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারবে কি না তা নিয়ে অমল সংশয়ী থাকে। সে তাই ছেলের দলের উপরেই ভরসা করে।
তারা রাজার ডাকহরকরাদের চেনে একথা শুনে সে তাদের বলে যে, পরদিন সকালে ছেলেরা যখন আসবে তখন তারা যেন সেই ডাকহরকরাদের একজনকে ডেকে এনে চিনিয়ে দেয়। এই প্রস্তাবের পূর্বভূমিকাতেই অমল ছেলের দলকে উদ্দেশ করে উল্লিখিত মন্তব্যটি করে।
১৪। “….তা হলে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে।” -কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা এ কথা বলেছেন? মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে ঠাকুরদা বলেছেন যে, অমলের পিসেমশাই মাধব দত্তের সঙ্গে যদি কবিরাজ এসে হাজির হন তাহলে তার মন্ত্রকে হার মানতে হবে।
ফকিরবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ ঘটে অমলের ঘরে। অমলের কথায় এই ফকির তাকে নানা দেশ-বিদেশের কথা বলে যান, যা শুনতে তার খুব ভালো লাগে। অমল যাঁকে ফকির জানে সে মাধব দত্তের কাছে ঠাকুরদা। অমলের কথার উত্তরে ফকির জানান যে, তিনি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলেন এবং তিনি এরকম যেখানে খুশি যেতে পারেন। অমল একথা শুনে উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে ওঠে এবং বলে যে, সে যখন ভালো হবে ফকির যেন তাকে তার চেলা করে নেন। ঠাকুরদা তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, বেড়াবার এমন মন্ত্র তিনি শিখিয়ে দেবেন যে, সমুদ্র-পাহাড়-অরণ্য কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু অমলের পিসেমশাই এবং কবিরাজমশাইয়ের কাছে তাঁর মন্ত্র পরাজিত হবে। আসলে ঠাকুরদা বা ফকির যে জীবনের সন্ধান দেন তার প্রতিষ্ঠা বৈষয়িকতার বাইরে। কিন্তু মাধব দত্ত চূড়ান্তভাবে বৈষয়িক। অমল আর ঠাকুরদার কথাকে তাই তার মনে হয় ‘পাগলের মতো কথা’। ঠাকুরদার মনোজগতে তাই মাধব দত্তের কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে কবিরাজ শাস্ত্রগ্রন্থকে অবলম্বন করে যেসব বিধান দেন সেখানে জীবনের কোনো সংযোগ ছিল না, বরং শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে জীবন-বিচ্ছিন্ন করার আয়োজন ছিল। ঠাকুরদার উদার-মুক্ত জীবনবোধের সঙ্গে মাধব দত্ত বা কবিরাজের জীবনাদর্শ একেবারে বেমানান ছিল। সেকারণেই ঠাকুরদা উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
১৫। “সে ভারি আশ্চর্য জায়গা।” -কে, কখন এই জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন? সেই জায়গার যে বর্ণনা বক্তা দিয়েছেন তা উল্লেখ করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে উল্লিখিত মন্তব্যটির বক্তা ঠাকুরদা। অমল ফকিরের কাছে জানতে চেয়েছিল সে কোথায় গিয়েছিল। ফকিররূপী ঠাকুরদা জানান যে, তিনি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলেন। তিনি যে ইচ্ছামতো যেখানে খুশি যেতে পারেন সে-কথাও জানান। অমল ঠাকুরদার চেলা হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে এবং জানতে চায় ক্রৌঞ্চদ্বীপ কীরকম দ্বীপ। এই সময়েই ঠাকুরদা উল্লিখিত মন্তব্যটি করেন।
ঠাকুরদার কথা মতো ক্রৌঞদ্বীপ এক আশ্চর্য দ্বীপ। সে হল পাখিদের দেশ, যেখানে মানুষ নেই। পাখিরা গান গায় আর ওড়ে। তারা ওড়ে সমুদ্রের ধারে আর নীল রঙের পাহাড়ে তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপরে সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে। আকাশের রং, পাখির রং, পাহাড়ের রং মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এখানে রয়েছে নৃত্যরতা ঝরনা। নুড়িগুলোকে নিয়ে আওয়াজ তুলে ঝরনাটি সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। ঠাকুরদার কথায় পাখিগুলো তাকে তুচ্ছ মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তাহলে তিনি সেই ঝরনার ধারে হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন।
১৬। “আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই-মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি…” -কখন বক্তা এ কথা বলেছে? সে কী দেখার কথা বলেছে? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে উল্লিখিত মন্তব্যটির বক্তা অমল। অমলের পিসেমশাই মাধব দত্ত অমলের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে অমল ফকির অর্থাৎ ঠাকুরদার কাছে জানতে চায়, ডাকঘরে তার নামে রাজার চিঠি এসেছে কি না। ঠাকুরদা উত্তর দেন যে, তিনি শুনেছেন রাজার চিঠি পথে আছে। অমল নিজেই তখন বলে যায় সেই পথের কথা। বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে যে ঘন বনের পথ দেখা যায়- সেই পথ। অমলের এই মন্তব্যে ঠাকুরদা বিস্মিত হন, সে সব জানে দেখে। সেই বিস্ময়ের নিরসনেই অমল উল্লিখিত মন্তব্যটি করে।
অমল বলেছিল যে, সে দেখতে পাচ্ছে রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা নেমে আসছে। তার বাঁ হাতে লণ্ঠন আর কাঁধে চিঠির থলি। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে, সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে। নদীর ধারে জোয়ারের খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে সে অবিরাম আসছে। তারপরে আখের খেত, তার পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে। সেই আলের উপর দিয়ে একলা রাতদিন অবিরাম চলে আসছে রাজার ডাকহরকরা। খেতের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। নদীর ধারে একটাও মানুষ নেই, শুধু কাদাখোঁচা ল্যাজ দুলিয়ে বেড়াচ্ছে। এই দৃশ্যপট যেন অমলের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। অমল যত দেখছিল, ততই খুশিতে তার মন ভরে উঠছিল।
"যেন সময় এসেছে আজ, ফুরালো মোর যা ছিল কাজ- বাতাস আসে হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে।” (৩৪, গীতাঞ্জলি)।
১৭। “তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে।” -কে, কোন্ প্রসঙ্গে মন্তব্যটি করেছে? এই মন্তব্যের কারণ কী? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন ঠাকুরদা। অমল ঠাকুরদার কাছে জানতে চেয়েছিল যে, তিনি রাজাকে জানেন কি না। ঠাকুরদা বলেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবেই রাজাকে চেনেন এবং প্রতিদিন তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যান। অমল তখন বলেছিল যে, সেও সুস্থ হয়ে উঠলে রাজার কাছে ভিক্ষা নিতে যাবে। ঠাকুরদা তখন বলেন যে, অমলের কোনো ভিক্ষার দরকার হবে না, রাজা অমলকে যা দেওয়ার এমনিই দিয়ে দেবেন। অমল তাতে রাজি না হয়ে বলে যে, সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাজার নাম করে ‘জয় হোক’ বলে ভিক্ষা চাইবে। এই প্রসঙ্গেই ঠাকুরদা বলেন যে, রাজার কাছে অমলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে তাঁরও পেটভরে ভিক্ষা মিলবে।
অমল এই বিশ্বসৌন্দর্যের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের আস্বাদ চায়। প্রাণের মুক্তির অপেক্ষা করে থাকে সে। প্রকৃতি ও প্রাণের সমগ্রতায় যে বিশ্বপ্রাণ, অমল তার নিমগ্ন উপভোক্তা। আর রাজা সেই মুক্তপ্রাণের আধার। তাই, ঠাকুরদার দৃষ্টিতে, অমল রাজার কাছে একান্তভাবে গ্রহণযোগ্য। রাজার কাছে অমলকে ভিক্ষা চাইতে হবে না, তিনি স্বেচ্ছায় অমলকে সমর্পণ করবেন। আর অমলের সঙ্গে রাজার সংযোগে প্রাণ ও সৌন্দর্যের যে অভিষেক হবে তা ঠাকুরদার কাছে এক পরমপ্রাপ্তি হবে। কারণ, তিনি নিজেই এই মুক্তপ্রাণের পুরোহিত।
১৮। “আমি তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াব।” -যে বিষয়ে বক্তা এ কথা বলেছে নিজের ভাষায় লেখো। যাকে নিয়ে এ কথা বলা হয়েছে তাকে নিয়ে বক্তা আর কী কী ভেবেছে? ২+৩
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা অমলের মধ্যে সুতীব্র। যখনই বাইরের পৃথিবীর কোনো না কোনো ইঙ্গিত কোনো সূত্রে তার কাছে এসেছে, তখনই সে সেটাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। ছিদাম অমলের কাছে বাইরের পৃথিবীর তেমনই এক ইশারা। অন্ধ, খোঁড়া সেই ব্যক্তি রোজ অমলের জানলার কাছে আসে। একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। সেই অমলকে বলেছে যে, অমল ভালো হয়ে উঠলে সে তাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। তার সঙ্গে অমল যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াবে।
অমল ছিদামকে বলেছে যে, ভালো হলে সে তাকে ঠেলে নিয়ে বেড়াবে। সেটাই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগের সেতু রচনা করবে। অমলের পিসেমশাই অমলকে বলে যে, ছিদাম হল ‘মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া’। কিন্তু অমল তা মানতে পারে না। ছিদাম ‘চোখে দেখতে পায় না’-এটা অমলের কাছে সত্যি। অমল ঠাকুরদাকে বলে যে সে ছিদামকে শোনায় কোথায় কী আছে। ঠাকুরদা অমলকে যেসব দেশের কথা শোনান সেগুলোও অমল ছিদামকে শোনায়। ঠাকুরদার বলা হালকা দেশের কথা শুনে ছিদাম খুব খুশি হয়েছিল। ছিদামের দুঃখ যে, সে কোনো কিছুই দেখতে পাবে না। তাকে সমস্ত জীবন শুধু ভিক্ষাই করে যেতে হবে। অমল তাকে সান্ত্বনা দেয় যে, ভিক্ষা করতে গিয়ে ছিদাম অনেক জায়গায় যেতে পারে, সকলে সে সুযোগ পায় না। এইভাবে অমলের ভাবনায় একদিকে ছিদামের প্রতি সহানুভূতি, অন্যদিকে তার বাধাহীন জীবনের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।
১৯। “ওটা একেবারেই ভালো নয়।” -কে, কোন্ বিষয়কে ‘একেবারেই ভালো নয়’ বলেছেন? এর কারণ কী ছিল? ২+৩
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে কবিরাজ উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছে। কবিরাজ বলেছিলেন যে, সেদিন একটা ‘কেমন হাওয়া’ বইছে, আর অমলদের বাড়ির সদর-দরজার ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে সেই হাওয়া বইছে, যা ‘একেবারেই ভালো নয়’।
কবিরাজ অমলের শরীরের খবর নিলে অমল বলেছিল যে, তার ‘খুব ভালো বোধ হচ্ছে।’ কিন্তু এই ‘ভালো বোধ হচ্ছে-‘কেই কবিরাজ ‘খারাপ লক্ষণ’ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সংশয় প্রকাশ করেন যে, অমলের মৃত্যু আসন্ন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও অমলের গায়ে বাইরের হাওয়া লেগেছে। অমলের পিসেমশাই মাধব দত্ত বলেন যে, তিনি চারদিক থেকে অমলকে আগলে রেখেছেন, তাকে বাইরে যেতে দেন না, দরজা প্রায়ই বন্ধ করে রাখেন। তখনই কবিরাজ সদর দরজা দিয়ে বাইরের হাওয়ার অনুপ্রবেশের কথা বলেন। মুক্তির সঙ্গে বদ্ধতার যে সংঘাত ‘ডাকঘর’ নাটকের কেন্দ্রে আছে, সেখানে কবিরাজ বদ্ধ জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেকারণেই কবিরাজ উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
২০। “…. আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি।” -কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা এ কথা বলেছেন? মন্তব্যটির নিহিত অর্থ আলোচনা করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে ঠাকুরদা উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন। মাধব দত্তের বাড়িতে এসে মোড়ল বিদ্রুপ করছিল, কারণ অমল বলেছিল তার কাছে রাজার চিঠি আসবে। মাধব দত্তকে ব্যঙ্গ করে সে বলেছিল যে, খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে। অমল যে রাজার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে ঘরে বসে আছে এবং সে জন্যই তাদের জানলার সামনে রাজার নতুন ডাকঘর বসছে, সেকথাও ব্যঙ্গের সঙ্গে জানায় মোড়ল। তার বিদ্রুপ তীব্রতর হয়ে ওঠে যখন মোড়ল একটা অক্ষরশূন্য সাদা কাগজ অমলকে দিয়ে বলে যে, সেটাই রাজার চিঠি এবং তিনি সেটা অমলকে পাঠিয়েছেন। মাধব দত্ত মোড়লকে এভাবে পরিহাস করতে নিষেধ করেন। এইসময়েই ঠাকুরদা বলেন যে, পরিহাসের সাধ্য মোড়লের নেই। মাধব দত্ত ঠাকুরদার আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করেন। “তুমিও খেপে গেলে নাকি!” তখনই ঠাকুরদা উল্লিখিত মন্তব্যটি করেন।
মোড়লের সাদা কাগজ ছিল অমলের রাজার চিঠি আসার প্রত্যাশার প্রতি বিদ্রুপ। কিন্তু ঠাকুরদা সেই সাদা কাগজেই অক্ষর খুঁজে পান এবং বলেন-“রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।” সাদা কাগজ শুধু অক্ষরহীনতাকে নির্দেশ করে না, তা এক সীমাহীন প্রসারতাকেও নির্দেশ করে। মুক্তপ্রাণের পুরোহিত ঠাকুরদা তাই সেখানে রাজার চিঠি দেখতে পান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পাগল’ প্রবন্ধে লিখেছেন “এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, ‘সেন্ট্রিফ্যুগল’ -তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন।” এই ক্ষ্যাপামিই ঠাকুরদাকে সাদা কাগজে রাজার চিঠি পড়ার ক্ষমতা দিয়েছে।
২১। “প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও-এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক……।” -কে, কখন এ কথা বলেছে? প্রদীপের আলো নিভিয়ে দেওয়া কোন্ বিশেষ তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করে? ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে উল্লিখিত মন্তব্যটির বক্তা রাজ-কবিরাজ। অমলদের বাড়িতে রাজার আগমনের খবর নিয়ে রাজদূত আসে। তারপরেই রাজ-কবিরাজের প্রবেশ ঘটে। তিনি অমলের ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা খুলে দিতে বলেন। অমল রাজ-কবিরাজকে বলেছিল যে, সে রাজাকে বলবে অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। পিসেমশাইকে সে বলে যে, রাজার কাছে সে চাইবে যে তিনি যেন তাকে তাঁর ডাকহরকরা করে দেন। এইসব কথা বলতে বলতেই অমলের ঘুম আসে। রাজ-কবিরাজ এই সময়েই বলেন যে অমলের ঘুম আসছে, তিনি তার শিয়রের কাছে বসবেন। এ কথা বলেই তিনি উল্লিখিত মন্তব্যটি করেন।
অমলের মৃত্যু আসলে প্রতীকী। এর মধ্য দিয়ে সে বদ্ধতা থেকে মুক্তির পথগামী হয়েছে। অমল চেয়েছিল নাগরাজুতো পরা কাজ খুঁজতে যাওয়া লোকটার মতো ঝরনার ধারে গিয়ে ছাতু খাবে। প্রহরীকে বলেছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে অনেক দূরের দেশে, যে দেশের কথা কেউ জানে না। ফকিরের দেখে আসা ক্রৌঞ্চদ্বীপ তার মন ছুঁয়ে থাকে। বাইরের জগতের জন্য এই বিস্ময়, নিরন্তর মানসভ্রমণের পরে যখন সে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেই সময়কে তার যাত্রার অনুকূল করে তোলার জন্যই রাজ-কবিরাজ প্রদীপ নিভিয়ে দিতে বলেছেন, তারার আলোয় অমলের নিরুদ্দেশ গন্তব্যের পথকে আলোকিত করতে চেয়েছেন।
২২। “আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই।” -বক্তা কখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছিয়েছে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে ঠাকুরদা প্রথম মোড়লের দেওয়া অক্ষরশূন্য কাগজে রাজার চিঠি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, রাজা স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন। তারপরেই সেখানে রাজদূতের আগমন ঘটে। অমলের কাছে রাজদূত খবর নিয়ে এসেছিল যে, সেদিন দুপ্রহর রাত্রে তার ঘরে রাজার আগমন ঘটবে। রাজার চিঠিকে সত্য প্রমাণ করে এরপরে রাজ-কবিরাজের আগমন ঘটে। তিনি এসেই সমস্ত বন্ধ দরজা জানলা খুলে দিতে বলেন। ‘গীতাঞ্জলি’র গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
"দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ মুরতি ধরিয়া জাগিয়া ওঠে আনন্দ; জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।"
একদিকে রাজার চিঠি এবং তাঁর আগমনের সম্ভাবনা, অন্যদিকে মুক্ত পরিবেশ, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পুনরায় সংযোগ-এই দুই মিলে অমলের ভালো লাগতে শুরু করে। সেই বোধ থেকেই সে উল্লিখিত মন্তব্যটি করে।
২৩। “তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।” -কে, কার সম্পর্কে এ কথা বলেছে? এই মন্তব্যের আলোকে উল্লিখিত ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে মাধব দত্ত ঠাকুরদা সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছে।
রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রায়শই কবি, সন্ন্যাসী বা ঠাকুরদার মতো চরিত্রদের আগমন ঘটে যাঁরা হয়ে ওঠেন নাট্যকারের ভাবনার বাহক। ‘রাজা’ নাটকে তিনি রাজার সখা, ‘শারদোৎসব’ নাটকে বালকদলের বন্ধু, ‘ডাকঘর’ নাটকে তিনিই অমলের সুহৃদ।
বিশ্বাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার যে সংযোগ ‘ডাকঘর’ নাটকের উপজীব্য, সেখানে ঠাকুরদা হলেন সূত্রধর। মাধব দত্ত তাঁকে ভয় করে এবং কারণ হিসেবে বলে, ” ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়ো বয়সের খেলা….” ঠাকুরদা অস্বীকার করেননি সে কথা। নিজেকে তিনি বলেছেন শরতের রৌদ্র আর হাওয়ার মতো ভয়ংকর এবং ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন যে, অমলকে তাঁর দরকার আছে, তিনি তাঁর সঙ্গে ‘ভাব’ করে নেবেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে ফকিরবেশে এই ঠাকুরদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে অমলের। তিনি তাকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের গল্প শুনিয়েছেন, সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্যকে অতিক্রম করে যাওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে দেবেন বলেছেন। ঠাকুরদার কথা শুনে অমল ‘পাখিদের দেশ’ ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখি হতে চেয়েছে। রাজা বিশ্বাত্মার প্রতীক, আর ঠাকুরদা তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যান। মনে রাখতে হবে বৌদ্ধ দর্শনে ভিক্ষু বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যিনি জাগতিক বিষয়বাসনা ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন। অমলের যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগের তৃয়া, তাকে ঠাকুরদাই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, রাজার কাছে অমলের ভিক্ষার দরকার হবে না,-” তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।” শূন্য কাগজে রাজার চিঠির অক্ষর ঠাকুরদাই পড়ে শোনান। রাজার আগমন সংবাদ অমলকে তিনি জানান। ঠাকুরদা এই নাটকে অমলের মনকে পরিচর্যা করেছেন। কবিরাজের বদ্ধ জীবনদর্শন কিংবা মাধব দত্তের বৈষয়িকতার বিপরীতে ঠাকুরদা এক বিকল্প জীবনদর্শনের পরিপোষক।
২৪। “এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ” -বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করেছেন? এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘ডাকঘর’ নাটকে যে নাট্যদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে দত্তক পুত্র অমলের অসুস্থতা নিয়ে চিন্তিত মাধব দত্ত কবিরাজকে ডেকে আনেন। কবিরাজ চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করে মূল যে কথাটা বলতে চান তা হল, অমলকে “খুব সাবধানে রাখতে হবে।” এই সাবধানে রাখার অর্থ তাকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, শরৎকালের রৌদ্র এবং বাতাস দুটোই অমলের জন্য ক্ষতিকারক।
ডাকঘর নাটকে দ্বন্দ্ব বদ্ধতার সঙ্গে মুক্তির, বস্তুসর্বস্বতার সঙ্গে কল্পনাপ্রবণতা ও সৌন্দর্যপিপাসার। অমলকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এই দ্বন্দ্ব। সেখানে বদ্ধতার প্রতীক কবিরাজ, মাধব দত্ত, মোড়ল প্রমুখ। কবিরাজ মনে করে অমলকে সুস্থ করতে হলে বাইরের আলো বাতাস লাগানো চলবে না। তাই তাকে দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরে রাখতে হবে। আর বিপরীতে আছেন ঠাকুরদা, নিজেকে যিনি মনে করেন শরতের রৌদ্র আর হাওয়ার মতো ভয়ংকর। যেখানে খুশি যেতে তাঁর কোনো বাধা নেই। এর মাঝখানে রয়েছে অমল। বস্তু পৃথিবী অমলকে বাইরের সঙ্গে মিলতে বাধা দেয়। অন্যদিকে অমল কখনও নাগরাজুতো পরা লোকটার মতো কাজ খুঁজতে যেতে চায়, দইওয়ালার ডাকে নিরুদ্দেশের আহ্বান শোনে, প্রহরীর ঘণ্টাধ্বনি অমলকে সময়ের সঙ্গে যেতে উৎসাহ দেয়। রাজার চিঠিতে থাকে নিরুদ্দেশের ইশারা। এই দ্বন্দ্বের উপসংহার ঘটে অমলের রাজার চিঠি পাওয়ায়।
২৫। ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল চরিত্রটি তোমার কীরূপ লাগে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।
উত্তর: কথামুখ: রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকের ‘অমল ধবল পালে’ চিরসুন্দরের সন্ধানী। স্থিতি বনাম গতি, বদ্ধতা বনাম মুক্তি, শাস্ত্রীয় অনুশাসন বনাম প্রাণের দ্বন্দ্বে অমলগতি, মুক্তি ও প্রাণের প্রতীক। রবীন্দ্রভাবনার সহজিয়া সুরে অমলের ‘হয়ে ওঠা’।
অমল পিতামাতৃহীন। মাধব দত্ত তাকে দত্তক নিয়েছে। কিন্তু অমলের প্রকৃত আশ্রয় বিশ্বব্রয়াণ্ডের অনন্ত বিস্তারে। তাই অসুস্থ অমল কবিরাজের নির্দেশে গৃহবন্দী থাকলেও জানলার সামনে বসে বাইরের পৃথিবীকে দেখে, তার সঙ্গে মিলতে চায়।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান: নাগরাজুতো পরে পাহাড়ের ওপারে কাজ খুঁজতে যায় যে লোকটি অমল তার মতো বেরিয়ে পড়তে চায়। দইওয়ালার ডাক তাকে উন্মনা করে দেয়। প্রহরী যেভাবে সময়ের বয়ে যাওয়ার সংকেত দেয় ঘণ্টা বাজিয়ে, তাও তার ভালো লাগে। এমনকি ভিক্ষাজীবী ছিদামের মতো সে দেশে দেশে ভিক্ষা করে বেড়াতে চায়, হতে চায় ফকিররূপী ঠাকুরদার চেলা। অমল যেন জীবনপথের চিরপথিক।
তোমার অমল অমৃত: শুধু পথচারী মানুষ নয়, উঠোনের প্রান্তে দু-হাত দিয়ে ডালের খুদ খায় যে কাঠবিড়ালি, অমল তার মতো হতে চায়। সে হতে চায় ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখি। জীবনের মুক্তছন্দ তাকে টানে।
কোন সাগরের পার হতে আনে/কোন সুদুরের ধন: রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা ছিল অমলের। সে চিঠি ঠাকুরদা কাহিনির শেষে পড়ে শুনিয়েছেন অমলকে। রাজার আসার খবর শুনিয়েছেন। ঠাকুরদা। রাজকবিরাজ বন্ধ দরজা জানলা খুলে দিতে বলেছেন। অমলের চোখে ঘুম নেমে এসেছে। এ যেন চেতনার নবপ্রস্থান। অসীম বিশ্বলোকে অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে যাত্রার প্রস্তুতি। প্রদীপের আলো নিভিয়ে দিয়ে তারার আলোয় আলোকিত সে যাত্রাপথ।
২৬। রূপক নাটক কাকে বলে? রূপক নাটক হিসেবে ‘ডাকঘর’-এর সার্থকতা আলোচনা করো। ২+৩
উত্তর : জোসেফ শিপলে তাঁর Dictionary of World Literature গ্রন্থে রূপক বা Allegory-র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-“A trope in which a second meaning is to be read beneath and concurrent with the surface story.” রূপক নাটকেও তাই বাইরের কাঠামোর আড়ালে থাকে আর-একটি কাহিনি, যা কখনও নীতিকাহিনি, কখনও বা জীবনের কোনো গভীরতর সত্য বা তত্ত্বকথাকে তুলে ধরে। সংকেত বা প্রতীক আবার নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কোনো ইশারা বা ব্যঞ্জনা। কোনো রূপক নাটকে নাট্যকার এই সংকেতের ব্যবহার করে থাকেন অনির্দেশ্যকে উপস্থাপনে, অপার্থিবকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।
‘ডাকঘর’ নাটকে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে সুন্দরের সঙ্গে মিলনের এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগের আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন। অমল নামের এক অসুস্থ কিশোর, তার জন্য কবিরাজের কঠোর নির্দেশ, গৃহবন্দি অমলের বাইরের জগতের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, রাজার চিঠির জন্য অপেক্ষা ইত্যাদি রয়েছে নাটকের বাইরের কাঠামোয়। সেই কাঠামোর আড়ালে রয়েছে কবিরাজের শাস্ত্রসর্বস্ব মানসিকতা, অমলের পণ্ডিত হতে না চাওয়া, নাগরাজুতো পরা লোকটার মতো অমলের কাজ খুঁজতে চাওয়া, দইওয়ালার ডাকে উদ্বেল হয়ে ওঠা ইত্যাদি। অমল নিজেই একটা রূপক চরিত্র। সে বন্ধনহীনতার রূপক। বস্তুজগতের বিধিনিষেধকে অতিক্রম করে যেতে চায় সে। কিন্তু এই রূপকার্থকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংকেতেরও সাহায্য নিয়েছেন নাট্যকার। ডাকঘর, ডাকহরকরা, রাজদূত কিংবা রাজকবিরাজ এই সংকেত বা সাংকেতিক চরিত্র হিসেবে কাজ করেছে। এরাই বহন করে এনেছে সেই অনির্দেশ্য জগতের ইশারা (রাজার চিঠি), যার মধ্যে অমল খুঁজে পেয়েছে আত্মার মুক্তি। নাটকের শেষে অমলের ঘুম আসা সেই প্রার্থিত অসীমে তার মুক্তির দ্যোতনা নিয়ে আসে। এইভাবে সংকেতের আশ্রয়ে ডাকঘর নাটকে রূপকধর্ম এক অসামান্য মাত্রা পেয়েছে।
২৭। কীভাবে রাজার চিঠি অমলের কাছে এসে পৌঁছোল ‘ডাকঘর’ নাটক অবলম্বনে তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকে প্রহরী অমলকে রাজার ডাকঘর তৈরির খবর দিয়ে বলেছিল যে, একদিন তার নামেও রাজার চিঠি আসবে। প্রহরী জানিয়েছিল যে, সেজন্যই অমলের খোলা জানলার সামনে রাজা একটা সোনালি রঙের নিশান উড়িয়ে ডাকঘর খুলেছেন এবং রাজার ডাকহরকরা অমলকে সেই চিঠি এনে দেবে। সেই থেকে শুরু হয় রাজার চিঠির জন্য অমলের অপেক্ষা। মোড়লকে সেই চিঠির কথা বলতে গিয়ে মোড়লের বিদ্রুপের মুখোমুখি হতে হয় অমলকে। ছেলের দলকে সে অনুনয় করে, যাতে ডাকহরকরার সঙ্গে তারা অমলের পরিচয় করিয়ে দেয়। ঠাকুরদা শেষপর্যন্ত অমলকে খবর দেন যে, অমলের চিঠি রওনা হয়েছে এবং সে চিঠি পথে রয়েছে। অতঃপর মোড়ল অমলকে একটা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়ে বিদ্রুপ করে যে, সেটাই রাজার চিঠি। আপাতভাবে এই আচরণকে নির্মম পরিহাস মনে হলেও ঠাকুরদা বলেন যে, মোড়লের পরিহাসের ক্ষমতাই নেই। অমল সরল বিশ্বাসে মোড়লকে বলে যে, মোড়ল যে রাজার চিঠি আনবে তা অমল কোনোদিনও মনে ভাবেনি। রাজার চিঠি হয়তো আক্ষরিকভাবে অমলের কাছে আসেনি, কিন্তু অমলের জন্য ঠাকুরদা উল্লিখিত চিঠির প্রতিটা অক্ষর প্রায় সত্যি হয়ে যায়। কারণ কিছু পরেই রাজ-কবিরাজ আসেন এবং তিনি রাজার আগমনের খবরও দেন।
২৮। ‘ডাকঘর’ নাটকে অমলকে কবিরাজ বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছিলেন কেন? অমলের সাথে ছেলের দলের কথোপকথন নিজের ভাষায় লেখো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে কবিরাজ অসুস্থ অমলকে খুব সাবধানে রাখতে বলেছিলেন, তার বাইরে বেরোনোতে তিনি একেবারে নিষেধ করেছিলেন। নাট্যকাহিনির একেবারে শেষ দিকে এসে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছেন সদর দরজা দিয়ে ভিতরে হুহু করে হাওয়া ঢুকতে দেখে। তাঁর মতে, সেটা একেবারেই ভালো লক্ষণ নয়। দরজা ভালো করে তালাচাবি বন্ধ করে দিতে হবে, জানলা দিয়ে যে সূর্যাস্তের আভা আসছে সেটাও বন্ধ করে রাখতে হবে, কারণ তা রোগীকে জাগিয়ে রাখে। কবিরাজ আসলে স্থিতি এবং বদ্ধতার প্রতীক। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে তাঁর চলাফেরা। তাই তাঁর কথায় বারে বারে উঠে আসে বিভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ধৃতি,-মহর্ষি চ্যবন থেকে চক্রপাণি দত্ত তাঁর উদ্ধৃতির বিষয় হয়। কিন্তু শাস্ত্রের বাইরে যে জীবন প্রসারিত সে জীবনের খোঁজ কবিরাজ রাখে না। সে কারণেই কবিরাজ দরজা-জানলা বন্ধ করার কথা বলে, বাইরে বেরোতে নিষেধ করে।
অমন জানলার সামনে দিয়ে ছেলের দলকে যেতে দেখে তারা কোথায় যাচ্ছে জানতে চায় এবং তাদের একটুখানি দাঁড়াতে বলে। ছেলেরা উত্তর দেয় যে তারা খেলতে চলেছে এবং তারা চাষ খেলা খেলবে। লাঠি দেখিয়ে একজন বলে যে, সেটা তাদের লাঙল আর একজন বলে যে, তারা দুজনে দুটো গোরু হবে। অমলের কথার উত্তরে তারা জানায় যে, সমস্ত দিন তারা খেলবে, তারপর সন্ধের সময় নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। অমল তাদেরকে অনুনয় করে ফেরার সময় তার ঘরের সামনে দিয়ে আসার জন্য। ছেলেরা তাকে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে খেলতে যেতে বলে, কিন্তু অমল জানায় যে কবিরাজ তাকে বের হতে নিষেধ করেছে। সে কবিরাজের মানা শোনে বলে ছেলেরা বিস্মিত হয়। অমল ছেলেদের বলে যে, তারা যেন তার জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করে। সেই খেলা সে দেখতে চায়। ছেলেরা প্রশ্ন করে যে, সেখানে তারা কী নিয়ে খেলবে। অমল তার সমস্ত খেলনা তাদের দিয়ে দিতে চায়, কারণ ঘরের ভিতরে তার একলা খেলতে ভালো লাগে না। সে সমস্ত খেলনা ধুলোয় ছড়ানো পড়ে থাকে, তার কোনো কাজে লাগে না। ছেলেরা সেইসব খেলনা, জাহাজ, জটাইবুড়ি, সুন্দর সিপাই দেখে বিস্মিত হয়। এবং অমল তাদেরকে খেলনাগুলি দিয়ে দিচ্ছে বলে তারা অবাক হয়ে যায়। অমল বলে যে সেই খেলনাগুলি তাদের আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, শুধু রোজ সকালে খেলনাগুলো নিয়ে তারা যেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু খেলা করে যায়। এরপরই অমলের ঘুম পায়, পিঠে ব্যথা শুরু হয়। সেই সময় এক প্রহরের ঘণ্টা বাজে। অমল ছেলের দলের কাছে জানতে চায় তারা রাজার ডাকঘরের ডাকহরকরাদের চেনে কি না। ছেলেরা বলে চেনে এবং তাদের একজনের নাম বাদল হরকরা, অন্যজনের নাম শরৎ, এরকম আরও আছে। অমল জানতে চায় যে, তার নামে যদি চিঠি আসে ডাকহরকরারা তাকে চিনতে পারবে কি না। ছেলেরা বলে যে, নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। অমল তাদের বলে পরের দিন সকালে তারা যখন আসবে ডাকহরকরাদের একজনকে ডেকে এনে ছেলেরা যেন তাকে চিনিয়ে দেয়। ছেলেরা অমলকে সেই প্রতিশ্রুতি দেয়।
২৯। ‘ডাকঘর’ নাটকের ঠাকুরদা চরিত্রটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঠাকুরদা, কবি, সন্ন্যাসী, পাগল প্রমুখ চরিত্র আসে জীবনের গভীরতর দর্শনের বাহক হিসেবে, যারা মূলত নাট্যকারের তত্ত্বভাবনার ধারক। ‘ডাকঘর’ নাটকের ঠাকুরদাও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজা নাটকে এরকমই এক ঠাকুরদা সুদর্শনাকে প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেছিল আত্ম-উপলব্ধির সহজ নিবিড়তায়। ‘ডাকঘর’ নাটকে স্বল্পপরিসরে ঠাকুরদার উপস্থিতি হলেও, অমলের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মিলবার এবং নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের জন্য যে আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে কবিরাজ, মাধব দত্ত বা মোড়লের মতো লোকেরা যখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠাকুরদা থেকেছেন অমলের সঙ্গে। কবিরাজ যখন বলেছেন যে শরতের রৌদ্র এবং হাওয়া অমলের জন্য বিষের মতো,
সেই সময় ঠাকুরদা নিজের সম্পর্কে বলেছেন, “একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো।” মাধব দত্ত তাকে বলেছিলেন ‘ছেলে খেপাবার সদ্দার’। আসলে যে জীবন বদ্ধতা এবং অনুশাসনে আটকে থাকে ঠাকুরদা সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখান।
নাট্যকাহিনির শেষপর্বে যেন নিজের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ঠাকুরদার আবির্ভাব ঘটে ফকিরের বেশে। সেই ফকির অমলকে বলেন যে, তিনি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলেন এবং তার কোনো জায়গায় যেতে কোনো বাধা নেই। অমল এসব শুনে তাঁর ‘চেলা’ হয়ে যেতে চায়। ঠাকুরদা জানান যে, পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র কোনো কিছুতেই তিনি ভয় করেন না, কিন্তু অমলের পিসেমশাই মাধব দত্ত আর কবিরাজ এলে যে তার মন্ত্রের হার হবে সে-কথাও তিনি জানান। কারণ, এই কবিরাজ এবং অমল দত্ত তাঁর কাছে বদ্ধতার প্রতীক। ঠাকুরদার কথায় ক্রৌঞ্চদ্বীপ ‘ভারি আশ্চর্য জায়গা’-পাখিদের দেশ। পাখিগুলো তাঁকে নিতান্ত তুচ্ছ মানুষ বলে একঘরে করে রেখেছিল, নাহলে ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে তিনি দিন কাটিয়ে দিতেন। অমল যে নির্বাধ জীবনের স্বপ্ন দেখে ঠাকুরদা যেন তার সওদাগর। ঠাকুরদাই অমলকে শোনান যে রাজার কাছে অমলকে ভিক্ষা নিতে হবে না, তিনি যা দেবার এমনিই দিয়ে দেবেন। অন্ধ খোঁড়া ভিখারিকে সে ঠেলে নিয়ে বেড়াবে শুনে ঠাকুরদা বলেন, ‘বেশ মজা হবে’। অর্থাৎ অমলের চিরসবুজ মনে যেন রঙের পোঁচ দিয়ে যান ঠাকুরদা। তিনি অমলকে বলেন যে, সেদিনই রাজার চিঠি আসবে।
যখন মোড়ল ব্যঙ্গ করে অক্ষরশূন্য চিঠিকে রাজার চিঠি বলে অমলকে দেয় তখন ঠাকুরদা চিহ্নিত করেন যে, সেটাই রাজার চিঠি। সে চিঠিতে লেখা আছে রাজা স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন এবং সঙ্গে রাজ কবিরাজকেও নিয়ে আসছেন। রাজা আসার আগে জানলা খুলে দেবার দায়িত্ব ঠাকুরদা-ই নেন। অমলের ঘুম পেলে রাজকবিরাজ যখন প্রদীপের আলো নিভিয়ে আকাশের তারার আলোকে আসার সুযোগ দিতে বলেন এবং মাধব দত্ত তাতে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন তোলেন, ঠাকুরদা বলেন-“চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কোয়ো না।” বিশ্বাস-অবিশ্বাস, জীবন-মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করে যে মহাজাগতিক সম্মিলন, যেখানে অমলের যাত্রা, ঠাকুরদা সেখানে যেন নির্দেশকের ভূমিকায়।
৩০। ” ‘ডাকঘর’ নাটকে আত্মার স্বাধীনতা বনাম শাসন-নিষেধের দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।”- আলোচনা করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকে যে মূল নাট্যদ্বন্দ্ব তা আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে অনুশাসনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব বদ্ধতার সঙ্গে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার, বস্তুসর্বস্বতার সঙ্গে কল্পনাপ্রবণতা ও সৌন্দর্যপিপাসার। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রয়েছে অমল, যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। আর বদ্ধতার প্রতীক হয়ে সেই ইচ্ছার বিপরীতে দাঁড়ায় কবিরাজ, মাধব দত্ত, মোড়ল প্রমুখ। কবিরাজ মনে করে অমলকে সুস্থ করতে হলে বাইরের আলো বাতাস লাগানো চলবে না। তাঁর মন্তব্য- “শরতকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ।” তাই তাকে দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরে রাখতে হবে। এর বিপরীতে আছেন ঠাকুরদা, নিজেকে যিনি মনে করেন শরতের রৌদ্র আর হাওয়ার মতো ভয়ংকর। যেখানে খুশি যেতে তার কোনো বাধা নেই। শাস্ত্রীয় অনুশাসন-নির্ভর বস্তুপৃথিবী অমলকে বাইরের জগতের সঙ্গে মিলতে বাধা দেয়। অন্যদিকে অমল কখনও নাগরাজুতো পরা লোকটার মতো কাজ খুঁজতে যেতে চায়, দইওয়ালার ডাকে নিরুদ্দেশের আহ্বান শোনে, প্রহরীর ঘণ্টাধ্বনি অমলকে সময়ের সঙ্গে যেতে উৎসাহ দেয়। আর অপেক্ষা করে থাকে রাজার চিঠি পাওয়ার। শেষপর্যন্ত মোড়লের দেওয়া অক্ষরহীন কাগজকে ঠাকুরদা চিহ্নিত করে দেন রাজার চিঠি বলে। রাজার চিঠিতে থাকে নিরুদ্দেশের ইশারা। রাজকবিরাজের উপস্থিতিতে সব দরজা-জানলা খুলে দেওয়ার পরে অমলের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। গ্রন্থপরিচয় অংশে ডাকঘর রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-” ‘ডাকঘর’ যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ উঠেছিল।… চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখ দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে।” দ্বন্দ্বের অবসানে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অমল তার মহাজাগতিক বিস্ময়ের উত্তরের কাছে পৌঁছে যায়।
আরো পড়ুন : উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টারের বাংলা প্রশ্ন উত্তর