তিমিরহননের গান কবিতার বিষয়বস্তু ও নামকরণের সার্থকতা
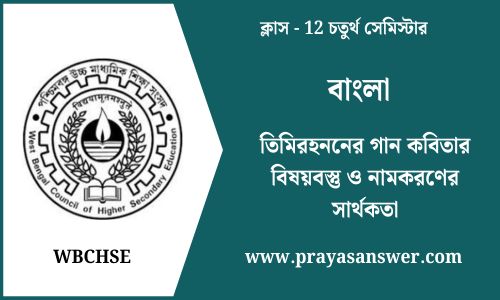
তিমিরহননের গান কবিতার বিষয়বস্তু
সমকালীন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংকট, জীবনের নানা অপূর্ণতা, বিচ্ছিন্ন কর্মজীবনের দীর্ঘ অনিশ্চয়তায় কবি জীবনানন্দ দাশের কলমে বারংবার সমাজজীবনের অন্ধকার দিকটি ফুটে উঠেছে। কবি সেই তিমির-সেই আঁধার থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গিয়েছেন মানবসভ্যতার আদি ইতিহাসে যখন প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে মানুষের আত্মিক বন্ধন ছিল, নিজেদের মধ্যে ছিল ভালোবাসার চিরন্তন সম্পর্ক। জীবন আসলে কী? এই জিজ্ঞাসার পথে মানুষ একে অপরের সঙ্গে জলের মতো মিশে এগিয়ে চলত সূর্যালোকের সহায়তায়। সেই পথে খুঁজে পেত অভিজ্ঞতা, প্রেম, সহমর্মিতা, সমৃদ্ধি। কিন্তু এর পরেই তার মনে আরও বেশি কিছু পাওয়ার লোভ ঘনিয়ে উঠল। যেখানে আকাশের মতো নির্মল, উদার দৃষ্টি নিয়ে মানুষ জীবনকে উপভোগ করত সেখানে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হল ক্ষমতার দম্ভে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবজাতি তারার আলোর মতো বহুদূরের মুক্তির আলোর দিকে মৃতের মতো নিষ্প্রভ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, যাদের অধিকাংশই তথাকথিত ‘ভদ্র-সাধারণ’। তারা সমকালীন মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ কোনো কিছু নিয়েই ভাবিত নয়, এক ধরনের দুঃখবিলাসিতায় তারা আচ্ছন্ন। কবি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিয়েই চিন্তিত। কারণ সমাজের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে তারা উদাসীন। চতুর্দিকে খিদের আগুন, লঙ্গরখানায় ক্ষুধার্ত মানুষের লম্বা লাইন, নর্দমা থেকে ওভারব্রিজ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মরণঘুম- কোনো কিছুই তাদের বিচলিত করে না। মধ্যমেধার অবিবেচক, আত্মকেন্দ্রিক, নিজের তৈরি করা কৃত্রিম দুঃখের বিলাসিতায় আচ্ছন্ন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নীরবতা ও ঔদাসীন্যই সামাজিক বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ সে-কথা বলা বাহুল্য। তবুও এই অন্ধকার সময়ে কবি মানবসভ্যতার অতীত ইতিহাসের উপর আস্থা রেখেছেন। যতবার মানুষ সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে ততবার সে আলোর সন্ধানে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার সময়ের করাল গ্রাস থেকে মানবসভ্যতার বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছে। তাই কবি সাময়িকভাবে হতাশ হলেও কবিতার শেষে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন- ‘আমরা তোতিমিরবিনাশী’।
তিমিরহননের গান কবিতার নামকরণের সার্থকতা
ভূমিকা: সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরিতে নামকরণের অন্যতম প্রধান ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রে কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবনা, কবির জীবনদর্শন এবং সমাজভাবনার আভাস পাওয়া যায়। কাজেই নাম, নামমাত্র নয়- তা হতে পারে বিষয়ানুসারী, চরিত্রানুসারী কিংবা ব্যঞ্জনাধর্মী। আবার বাংলা সাহিত্যে অনেক নামহীন কবিতার নিদর্শনও আছে। যেমন আমাদের আলোচ্য পাঠ্য ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর অধিকাংশ কবিতারই নামকরণ করেননি। সেক্ষেত্রে সেই কবিতার প্রথম পঙ্ক্তিটি কিংবা তার কিয়দংশ শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও আলোচ্য ‘তিমিরহননের গান’ কবিতাটি তার ব্যতিক্রম এবং সেই কারণেই এই নামকরণ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।
বিশ্লেষণ: ‘তিমিরহননের গান’ কবিতাটির পটভূমি প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কাল এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বিপন্ন সমাজব্যবস্থা এবং নৈতিকতার চরম অবনতির প্রেক্ষাপটে রচিত এই কবিতার মুখ্য বিষয় হল সামাজিক অবক্ষয়ের অন্ধকারকে বিনাশ করে মানবচেতনার জাগরণ। কবিতায় ‘তিমির’ শব্দটি শুধু রাতের অন্ধকারকে বোঝায় না- এটি প্রতীক হয়ে উঠেছে সমাজের অজ্ঞতা, হতাশা এবং মানবতার বিপর্যয়ের। ‘তিমির’ এখানে মানবসভ্যতার উপর ঘনিয়ে আসা নৈরাজ্যের অন্ধকার। ‘হনন’ শব্দটি সেই তিমিরকে নাশ করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর ‘গান’ মানে আমাদের অন্তরের সেই সুর যা কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়ে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে- সমস্ত মলিনতাকে মুছে সেই সংগীত নিয়ে আসে আনন্দের আলো। কবি সচেতনভাবেই মানবতার সেই জয়গানে সকলকে গলা মেলাতে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে স্বার্থপর, শোষক শ্রেণির আগ্রাসনে বঙ্গদেশে নেমে এসেছিল ভয়াল দুর্ভিক্ষ। সার্বিক মানবিক চেতনা হয়েছিল অবলুপ্ত। তথাকথিত ‘ভদ্র-সাধারণ’-এর অবহেলায় বৃহত্তর শোষিত জনগোষ্ঠী বঞ্চনার আঁধারে তলিয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মানবতার পূজারি কবি জীবনানন্দ ‘অন্তহীন বেদনার পথে’ ‘বেদনাহীন’ – হয়ে থাকতে পারেননি। সমবেদনায় কাতর হয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন-
"আমরা তো তিমিরবিনাশী হ'তে চাই। আমরা তো তিমিরবিনাশী।"
কবির এই সোচ্চার ঘোষণা যেন হতাশা ও বিপন্নতার মাঝে জীবনের আলো স্বরূপ প্রতীত হয়েছে। তাঁর এই বার্তা আসলে সমস্ত ধরনের নেতিবাচক শক্তিকে বিনষ্ট করে আলোর পথে, সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা।
সার্থকতা: আলোচ্য ‘তিমিরহননের গান’ কবিতাটি কবি জীবনানন্দ দাশের বক্তব্য এবং সমকালীন সমাজবাস্তবতার এক প্রতিচ্ছবি। সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়ের আঁধারকে দূরীভূত করার প্রয়াস এই কবিতায় গভীর ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই কবিতার ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ সার্থক হয়েছে।